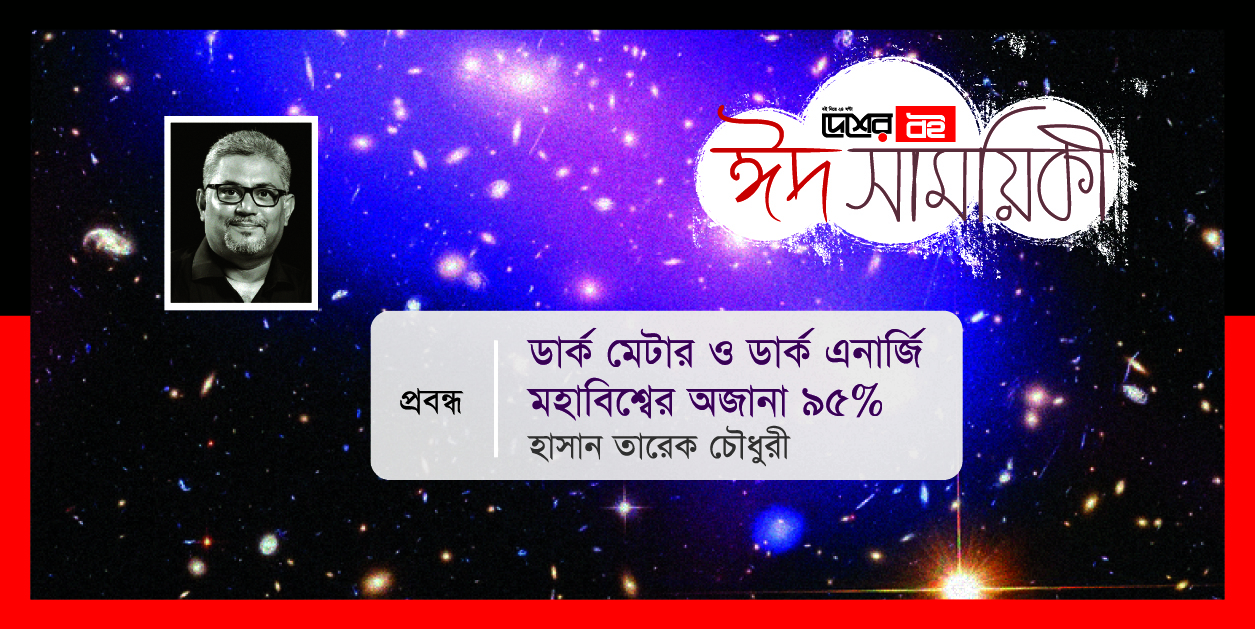
ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি : মহাবিশ্বের অজানা ৯৫%
॥ হাসান তারেক চৌধুরী ॥
রহস্যময় পঁচানব্বই
ধরুন আপনি হঠাৎ করে জানতে পারলেন, আমাদের এই বিশাল মহাবিশ্বে আমদের চেনা-জানা যা কিছু আছে, তা আসলে মহাবিশ্বের খুবই সামান্য অংশ, তাহলে আপনার অনুভূতি কি হবে? আলোচনাটাই বা কি রকম হবে?
আপনি হয়তো প্রথমেই জানতে চাইবেন, এই চেনা-জানা “বস্তু” বলতে আমি আসলে কি বুঝাতে চাইছি?
উত্তরঃ খালি চোখে বা সবচেয়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপ ও আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে আমরা যা কিছু দেখতে পাই, যেমনঃ গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি, নীহারিকা, ব্ল্যাকহোল, মহাজাগতিক মেঘ ইত্যাদি সব কিছু।
প্রশ্নঃ খুব সামান্য অংশ বলতে আসলে কতটুকু অংশ?
উত্তরঃ আমাদের জানা সবকিছু মিলে মহাবিশ্বের মাত্র ৫% উপাদান!
নিঃসন্দেহে এবার আপনি নড়েচড়ে বসবেন। জানতে চাইবেন, “বাকী ৯৫% তাহলে কি?”
বিজ্ঞানীরা বলবেন, “আমরা এখনো এই সম্পর্কে তেমন কিছুই জানিনা। এদের দেখা যায় না, পরীক্ষাগারে গবেষণা করা যায় না, আমাদের চেনা জানা কোন কোন বস্তুর সাথে এর কোনো মিল নেই! এই ৯৫% হলো সম্পূর্ণ রহস্যময় ও অদৃশ্য এমন কোনো বস্তু ও শক্তি, যাদের সম্পর্কে আমাদের তেমন কোনো ধারণাই নেই।
অনেকে হয়তো কথাটি হেসেই উড়িয়ে দিতে চাইবেন, কেউ হয়তো অবিশ্বাস নিয়ে বলবেন, “দূর, তাই কি হয়? এত কিছু মিলে মাত্র ৫% বস্তু বা আমাদের চেনা-জানা পদার্থ!”
কিন্তু বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারটিতে একেবারেই নিরুপায়, তারা জানেন অবিশ্বাস্য হলেও এই বিপুল পরিমাণ অজানা উপাদানের অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এই শতকে এটাই জ্যোতিঃপদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিদগনের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সারা পৃথিবীব্যাপী বিজ্ঞানীরা যেন এক উন্মাদ প্রতিযোগিতায় নেমেছেন এদের খোঁজ পেতে, এদের একটি মাত্র কণা হলেও খুঁজে পাতে। মটির নীচ থেকে মহাকাশ, অবিরাম তারা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন এই অদৃশ্য বস্তুর খোঁজে। আর তারা যত বেশি চেষ্টা করছেন, যত উন্নত যন্ত্র ব্যবহার করছেন, ততই তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে য, এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান কতই-না নগণ্য! তারা জানেন, যেদিন সত্যিই এই রহস্যময় জিনিসটির একটি মাত্র কণা বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে সনাক্ত করতে পারবেন, সেই দিনটি হবে আমাদের এই মহাবিশ্বের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দিন।
কিন্তু কেনই-বা বিজ্ঞানীরা রহস্যময় অদৃশ্য এই জিনিসটির অস্তিত্বের বিষয়ে এতটা নিশ্চিত?
কারণ, মহাবিশ্বে যদি এই রহস্যময় অদৃশ্য জিনিসটি না থাকতো তাহলে আমাদের মহাবিশ্ব অন্যরকম হতো, নক্ষত্রগুলোকে গ্যালাক্সির ভিতরে আর গ্যালাক্সিগুলোকে ক্লাস্টারের ভিতরে ধরে রাখা সম্ভব হতো না। নক্ষত্রগুলো গ্যালাক্সি থেকে ছুটে বের হয়ে গিয়ে মহাশূন্যে হারিয়ে যেত। বিশৃঙ্খল এক অবস্থা তৈরি হতো। এই অবস্থায় হয়তো প্রাণীজগৎ সৃষ্টি হওয়ার মতো উপযুক্ত কোনো প্রবেশ তৈরি হতে পারতো না। তখন এমন কোন প্রানীও মহাবিশ্বে জন্ম নিতো না, যে কি-না প্রশ্ন করতে পারে – আমাদের এই মহাবিশ্বের উপাদান কি?
বদলে যাওয়া ধারণা
ছেলেবেলায় বা কৈশোরে পদার্থ এবং পরমাণু সম্পর্কে স্কুলে আমরা যা শিখেছি, তা অনেকটা এরকমঃ আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে যেমনঃ কলম, খাতা, বই, চেয়ার-টেবিল, গাছপালা, মাটি, পানি, চাঁদ-সূর্য, এমনকি মানুষ, সহ অন্যান্য সব প্রাণীও এক ধরণের পদার্থ। শুধু তাই-ই নয়, আমাদের এই সৌরজগত, নক্ষত্র মন্ডলী, নীহারিকা, বিলিয়ন বিলিয়ন গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ সবকিছুই আসলে একধরণের পদার্থ। আর এই পদার্থগুলোকে ভাঙতে ভাঙতে যে ক্ষুদ্রতম অংশ পর্যন্ত পদার্থটির বিশেষ রাসায়নিক গুনাবলি অক্ষুন্ন থাকে তাকে বলা হয় ঐ পদার্থের অণু। এই অণুগুলো আবার বিভিন্ন রকম পরমাণু সমন্বয়ে তৈরি। আমরা জেনেছি এই অকল্পনীয় বিশাল মহাবিশ্বের যত বস্তু, ক্ষুদ্র বালুকণা থেকে বিশাল গ্যালাক্সি সব কিছুই তৈরি এই পরমাণু দিয়ে।
অতি আনুবীক্ষনিক এই পরমাণু আসলে কী, আর কিভাবেই সে এই বিশাল মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তু তৈরি করেছে, এই বিষয়গুলো যখন আমাদের কিশোর মস্তিস্ককে সবে নাড়া দিতে শুরু করেছে, ততদিনে বিজ্ঞানীরা সম্মুখীন হয়েছেন নতুন এক অজানা জগতের – এক অবিশ্বাস্য সত্যের। তারা জানতে পেরেছেন যে, এই বিশাল মহাবিশ্ব শুধুমাত্র পরমাণু বা এটম দিয়েই তৈরি নয়, বরং এর বিরাট একটা অংশই এক বিস্ময়কর ও রহস্যময় কোনো উপাদান দিয়ে তৈরি, যার সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই নেই। আমাদের চারপাশ এই রহস্যময় উপাদান দিয়ে পরিপূর্ণ, এগুলো আমাদের আশেপাশেই আছে – কিন্তু আমরা সরাসরি, এমনকি গবেষণাগারেও কোনভাবেই তাদের দেখতে পারিনা!
বিজ্ঞানীদের বিস্ময়ের মূল কারণ অবশ্য আরো অনেক গভীরে। উপাদানটির প্রকৃতি নিয়ে তাদের যতটা না বিস্ময়, তার চেয়েও অনেকগুণ বেশি বিস্ময় মহাবিশ্বে এর পরিমাণ নিয়ে। বিজ্ঞানীরা যখন মহাবিশ্বে এদের সম্ভাব্য পরিমাণ গণনা করে বের করলেন, যেদিন তারা জানতে পারলেন মহাবিশ্বের ৯৫% ভাগই হলো বিস্ময়কর ও রহস্যময় অজানা উপাদান, সেদিন যেন তারা সত্যি সত্যিই বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।
বিষয়টির তাৎপর্য বুঝে নিতে আমরা প্রথমে দেখি আমাদের জানা মহাবিশ্ব আসলে কি কি দিয়ে গঠিত। দৃশ্যমান মহাবিশ্বে গ্যালাক্সির সংখ্যা আনুমানিক ২ ট্রিলিয়ন। বোঝার সুবিধার জন্য ট্রিলিয়ন সংখ্যাটা কর বড়, সেটিও স্মৃতি থেকে একটু ঝালিয়ে নেই।
১০ লক্ষ = ১ মিলিয়ন
১০০০ মিলিয়ন = ১ বিলিয়ন
১০০০ বিলিয়ন = ১ ট্রিলিয়ন
আমাদের এই ২ ট্রিলিয়ন গ্যালাক্সিতে নক্ষত্রের আনুমানিক সংখ্যা (১ X ১০২৪), যা আমাদের সমগ্র পৃথিবীতে যতগুলো ধুলিকণা আছে তার চেয়েও বেশি। আমাদের সূর্য একটি মাঝারি আকারের নক্ষত্র, এই মাঝারি আকারের নক্ষত্রটিও আমাদের পৃথিবী থেকে তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার গুন বড়। এই বিশাল সংখ্যক নক্ষত্রের অনেকেরই আমাদের মতো সৌরজগত রয়েছে, তার সাথে প্রতিটিতে রয়েছে লক্ষ লক্ষ ধুমকেতু ও অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তু। অধিকাংশ মহাবিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে আতিকায় (সুপার ম্যাসিভ) সব ব্লাকহোল। এম৮৭ গ্যালাক্সির বিখ্যাত ব্লাকহোলটির ভর সূর্যের প্রায় ৬.৫ বিলিয়নগুন বেশি। এ পর্যন্ত জানা সবচেয়ে বড় ব্ল্যাকহোলটির ভর প্রায় ২১ বিলিয়ন সূর্যের সমান। এগুলো ছাড়াও মহাবিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে ছোট বড় আরও অসংখ্য ব্ল্যাকহোল, অগনিত নীহারিকা, আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস, ধুলিকণা, প্লাজমা, এন্টিম্যাটার ইত্যাদি। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, মহাবিশ্বের যে সব বস্তুর কথা এ পর্যন্ত বলা হলো সেগুলো সম্মিলিতভাবে তৈরি করে মহাবিশ্বের মাত্র ৫% অংশ।
বাকী ৯৫% তাহলে কী?
রহস্যময় অজানা উপাদান, যার সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই নেই! কি এর আকৃতি, প্রকৃতি, গঠন কিছুই জানা নেই আমাদের। গত কয়েক দশক ধরে বিজ্ঞনীরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন এইসব প্রশ্নের উত্তর। এখনো পর্যন্ত শুধু এতটুকুই বলা যায় যে, বাকি এই ৯৫% তৈরি হয়েছে আমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে অজানা ও অচেনা দুইটি উপাদান দিয়ে – বিজ্ঞানীরা যাদের নাম দিয়েছেন ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি! এদের মধ্যে ২৫% হলো ডার্ক ম্যাটার আর বাকি ৭০% হলো ডার্ক এনার্জি। মজার ব্যাপার হলো, যে ৫% পদার্থকে আমরা “নরমাল ম্যাটার” বা “স্বাভাবিক পদার্থ” বলে চিনি, সত্যিকারভাবে বলতে সেটাই আসলে আমাদের মহাবিশ্বে “অ্যাবনরমাল” – পরিমানগত হিসেবে ভীষণভাবে সংখ্যালঘু।

প্রাথমিক ধারণা নেয়ার জন্য এখানে মহাবিশ্বে সাধারণ বস্তু বা ম্যাটার, ডার্ক ম্যাটার, ডার্ক এনার্জির একটি তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে রহস্যময় এই ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জির খোঁজে বিজ্ঞানীদের নানা রকম গবেষণাগুলো এবং তার উপর ভিত্তি করে আমরা এখনো পর্যন্ত যতটুকু জানতে পেরেছি, তার একটি সাধারণ ধারণা নেয়ার চেষ্টা করবো।
২
ডার্ক ম্যাটার
ডার্ক ম্যাটার জিনিসটা আসলে কী?
এই প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানীদের জানা নেই। তারা বরং বলতে পারবেন কোন কোন বস্তু ডার্ক ম্যাটার না।
প্রথমত, এটি গ্রহ, সাধারণ নক্ষত্র, সাদা বামন, নিউট্রন নক্ষত্র বা এ জাতীয় কোনো কিছু নয়। দ্বিতীয়ত, এটি আমাদের চেনা জানা সাধারণ বস্তুদের কোন ভিন্ন রূপ অথবা কালো অন্ধকার গ্যাসীয় মেঘও নয়। তৃতীয়ত, এটি এন্টিম্যাটার নয়, কারণ সেক্ষেত্রে এটি সাধারণ ম্যাটারের সাথে সংঘর্ষে গামা রশ্মি তৈরি করতো, যা বিজ্ঞানীরা দেখতে পেতেন, এবং চতুর্থত, এটি ব্ল্যাকহোল বা এরকম কিছুও নয়।
প্রশ্নটা তাহলে আবারো উঠে আসে, এটি আসলে কি?
পৃথিবীর প্রায় সব জ্যোতির্বিদগনের কাছেই প্রশ্নটির উত্তর নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় আরাধ্য বিষয়।

শুরুর ইতিহাস
ডার্ক ম্যাটারের ধারণাটি যে একেবারে নতুন, এমন কিন্তু নয়। বিষয়টি প্রথম আলোচনায় আসে গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে, সুইস-আমেরিকান জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানী ফ্রিৎজ জুইকির (Fritz Zwicky) মাধ্যমে। ১৯৩৭ সালে তিনিই প্রথম এর অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুমান করেন। কোমা ক্লাস্টার (Coma Cluster) নামে পরিচিত একটি গ্যালাক্সি গুচ্ছের ভেতরের প্রায় ১০০০ গ্যালাক্সির গতিবিধি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিলেন ফ্রিৎজ। তখন তিনি এই গ্যালাক্সিগুলোর আচরনে অদ্ভুত একটি ব্যাপার লক্ষ্য করেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, গ্যালাক্সিগুলো স্বাভাবিক গতির চেয়ে অনেক বেশি গতিতে এই গুচ্ছের মধ্যে পরিভ্রমণ করছে।
গ্যালাক্সিগুলোর এই অস্বাভাবিক গতিবেগ লক্ষ্য করে ফ্রিৎজ ক্লাস্টারের সবগুলো গ্যালাক্সি ও অন্যান্য সব মহাজাগতিক বস্তুর সম্মিলিত ভর নানাদিক থেকে নানাভাবে হিসেব করে দেখলেন। এই উপাত্ত ব্যাবহার করে ক্লাস্টারের মহাকর্ষ ক্ষেত্রের শক্তিমত্তার যে হিসেব তিনি পেলেন, সেটি ব্যবহার করে ক্লাস্টার থেকে গ্যালাক্সিগুলোর সম্ভাব্য মুক্তি বেগের একটি হিসাব তিনি বের করলেন। তিনি বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন ক্লাস্টারের ভেতরের মুক্তিবেগের (Escape Velocity) চেয়ে গ্যালাক্সিগুলোর গতিবেগ অনেকগুণ বেশি! এই বেগে গ্যালাক্সিগুলো কয়েক বিলিয়ন বছর আগেই ক্লাস্টার থেকে ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার কথা! কিন্তু বাস্তবে যেহেতু তা ঘটেনি, তাই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ঐ গ্যালাক্সি ক্লাস্টারে এমন কোন অদৃশ্য বস্তু লুকিয়ে আছে যা মহাকর্ষ ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় “অতিরিক্ত” ভরটুকু জোগান দিচ্ছে, ফলে গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে এবং গ্যালাক্সিগুলো ক্লাস্টার থেকে ছুটে বের হয়ে যেতে পারছে না। তিনি এই অদৃশ্য বস্তুটির নাম দিলেন “ডার্ক ম্যাটার”- সময়টা ছিল ১৯৩৭ সাল।
ফ্রিৎজের এই তত্ত্ব প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সারা ফেললেও পরবর্তী তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এটি মূলধারা বৈজ্ঞানিক আলোচনার আড়ালে চলে যায়। বিষয়টি নিয়ে আবার নতুন করে আলোচনা শুরু হয় ১৯৭০ এর দশকে দুজন আমেরিকান জ্যোতির্বিদের কাজের সূত্র ধরে। জ্যোতির্বিদ ভেরা রুবিন (Vera Rubin) ও তার সহযোগী গবেষক কেন্ট ফোর্ড (Kent Ford) মহাকাশে গ্যালাক্সিগুলোর গতিবিধি ও তাদের ঘুর্ণন বেগ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। গ্যালাক্সিগুলোর কৌনিক ঘূর্ণনের যে গ্রাফ বা লেখচিত্র তারা পেলেন, তাতে তারা প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে প্রাপ্ত ফলাফলের এক বড় ধরনের অসংগতি লক্ষ্য করলেন।
নিউটনের সূত্র অনুসারে, যে গ্রহটি সূর্য থেকে যত দূরে অবস্থিত, সূর্যের চারিপাশে তার ঘূর্ণন বেগ তত কম হবে। আমাদের সৌরজগতের গ্রহগুলোর তা সত্যি বলে প্রমানিত হয়েছে। যেমন, সূর্যের চারিপাশে আবর্তনের ক্ষেত্রে বুধ গ্রহের চেয়ে পৃথিবীর গতিবেগ কম, তেমনি পৃথিবীর চেয়ে বৃহস্পতি গ্রহের গতিবেগ আরও কম। নিচে একটি চার্টের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো হলোঃ

ভেরা রুবিন ও কেন্ট ফোর্ড যখন অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির নক্ষত্রগুলোর গতিবেগ পরিমাপ করেছিলেন, তারা আশা করেছিলেন যে গ্যালাক্সির নক্ষত্রগুলোও একই নিয়ম মেনে চলবে, অর্থাৎ গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে যে নক্ষত্র যতবেশি দূরে হবে তার ছুটে চলার গতি ধারাবাহিক হারে তত কম হবে। এরকম ঘটার কারণ নক্ষত্রটি যত দূরে হবে, তার উপর গ্যালাক্সির মহাকর্ষ বলের প্রভাব তত কম হবে, ফলে তার গতিবেগও তত কম হবে। কিন্তু, তাদের গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্ত যখন হাতে পেলেন, রীতিমত বিস্মিত হয়ে গেলেন তারা। ভেরা ও কেন্ট দেখতে পেলেন, গ্যালাক্সিগুলোর ভেতরে নক্ষত্রগুলো নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অনুসরণ করছে না! গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে নক্ষত্রগুলোর দূরত্ব যাই হোক না তাদের ছুটে চলার গতিবেগে উল্ল্যেখযোগ্য কোনই পার্থক্য নেই! অর্থাৎ, গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে কাছের ও বহু দূরে অবস্থিত নক্ষত্রগুলো একই রকম দ্রুত গতিতে ছুটে চলছে!
ভেরা ও কেন্টের কাছে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ালো, “সৌরজগতের গ্রহগূলোর জন্য মহাকর্ষ বলের যে নিয়ম নির্ভুলভাবে কাজ করছে, গ্যালাক্সির অভ্যন্তরে নক্ষত্রের ক্ষেত্রে সেই নিয়ম খাটছে না কেনো? তাহলে কি গ্যালাক্সির মতো বৃহত্তর পরিসরে নিউটনের সূত্রের কোনো সংশোধনী প্রয়োজন? নাকি অন্য কোন বিশেষ কারণ নক্ষত্রগুলোর আচরণের জন্য দায়ী?”
নক্ষত্রগুলোর এই অদ্ভুত আচরণের মাত্র দুটি মাত্র ব্যাখ্যা তাদের সামনে ছিলো। প্রথম ব্যাখ্যাটি হলো, বৃহত্তর পটভূমিতে নিউটনের সূত্র যথাযথ ভাবে কাজ করে না এবং এর সংশোধনী প্রয়োজন। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি হলো, গ্যালাক্সির ভেতরে অদৃশ্য ও অজানা এমন কিছু লুকিয়ে রয়েছে, যা বাড়তি “ভরের” জোগান দিয়ে নক্ষত্রগুলোর এই অস্বাভাবিক গতির জন্য প্রয়োজনীয় বাড়তি “মহাকর্ষ বলের” জোগান দিচ্ছে।
ভেরা ও কেন্ট জানতেন নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রটি কয়েক শতাব্দী প্রাচীন একটি পরীক্ষিত সূত্র, তাই তারা দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই মেনে নিলেন। তারা বললেন, গ্যালাক্সি ও সারা মহাবিশ্বব্যাপী এমন কিছু অদৃশ্য ও লুকানো “ভর” ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যা নক্ষত্র ও গ্যালাক্সিগুলোর এই অস্বাভাবিক গতির জন্য দায়ী। এর মাধ্যমেই সদর্পে ফিরে এলো ফ্রিৎজ জুইকির “ডার্ক ম্যাটারের” ধারণাটি এবং সূচনা হলো জ্যোতির্বিদ্যার জগতে এক নতুন যুগের।
অদৃশ্যকে আবিষ্কারের প্রতিযোগিতা
একটি প্রশ্ন এখানে অবধারিতভাবেই আসতে পারে যে, সরাসরি বা গবেষণাগারে, কোনভাবেই যদি এদের দেখতে পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে বিজ্ঞানীরা কিভাবে এটির অস্তিত্ব সম্পর্কে এতটা নিশ্চিত হলেন? এমন একটি কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করা কি আসলেই সম্ভব?
হ্যাঁ, এমন কিছুর অস্তিত্ত্ব প্রচলিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই নির্ণয় করা সম্ভব।
“কীভাবে?”
পরোক্ষভাবে পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে।
আমরা কোন বস্তুকে কিভাবে দেখতে পাই?
কোনো একটি বস্তুর উপর আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে যখন আমাদের চোখের রেটিনা অথবা আলোক সংকেত গ্রহণ করতে সক্ষম এমন কোন যন্ত্রের উপর আপতিত হয়, তখনই আমাদের মস্তিষ্কে বা যন্ত্রের ভিতরে বস্তুটির একটি প্রতিবিম্ব তৈরি হয় এবং আমরা বস্তুটিকে দেখতে পারি। আবার কোন কিছু যদি নিজেই আলোর উৎস হয় তাহলেও একই পদ্ধতিতে আমরা তাঁকে সরাসরি দেখতে পারি। একে আমরা বলি প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষন।
কিন্তু ডার্ক ম্যাটার নিয়ে নিয়ে সমস্যা হলো এটি নিজে কোন আলো নির্গত করে না, অথবা কোন প্রকার আলোক তরঙ্গ প্রতিফলিত করে না। আলো সরাসরি একে সম্পূর্ণভাবে ভেদ করে চলে যায়। এটি সত্যিকার অর্থেই একেবারে নিকষ কালো একটা বস্তু বা উপাদান। তাই এর অস্তিত্ব নিরূপন করার এবং একে দেখার একমাত্র উপায় হচ্ছে পারিপার্শ্বিক এলাকায় এর প্রভাব দেখে ও তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষন করার মাধ্যমে।
ধরা যাক, আপনি একটি রেস্তোরাঁয় বসে চা পান করছেন। টেবিলের ওপাশে কোন মানুষ বা অন্য কিছু নেই। হঠাৎই বলা নেই, কওয়া নেই টেবিলের ওপাশে রাখা একটি খালি কাপ নিজে থেকেই নড়ে উঠল। তারপর এমনভাবে নড়াচড়া শুরু করলো যেন কেউ ওটাতে চা খাচ্ছে। আপনার অনুভূতি কি হবে তখন? নিশ্চিতভাবে চমকে উঠবেন আপনি, হয়তো লাফিয়ে উঠবেন। কারণ এভাবে নিজে থেকে একটি কাপ নড়ে উঠতে পারেনা, ওখানে কিছু একটা আছে, যেটিকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। ওটাকে আপনি ভৌতিক কিছুই ভাবুন অথবা বৈজ্ঞানিক কোনো ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টাই করুন, নিশ্চিতভাবেই ওই স্থানে অজানা একটা কিছুর অস্তিত্ব আপনি মেনে নিবেন। ঠিক একইভাবে অন্য বস্তু বা পারিপার্শ্বিকের উপর এর প্রভাব প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে পরোক্ষ পদ্ধতিতে বিজ্ঞানীরা ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জির অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন।
সময়টা ১৯৮৫ সাল। তরুণ ফরাসী জ্যোতির্বিদ ইয়ানিক মেলিয়র (Yannik Mellier) পাড়ি জমিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের উদ্দেশ্যে। সেখানে তিনি যাচ্ছেন সমুদ্রপৃষ্ট থেকে ৪,২০০ মিটার উচ্চতায় মাউনা কিয়া (Mauna Kea) আগ্নেয়গিরির উপরে অবস্থিত মানমন্দিরে (Observatory) এক বিশেষ প্রজেক্টের অংশ হয়ে। তাদের লক্ষ্য হলো মানমন্দিরে অবস্থিত পৃথিবীর অন্যতম সেরা টেলিস্কোপের সাহায্যে দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলোর অবস্থা ও অবস্থান সংক্রান্ত নানারকম পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা করা।
হঠাৎ করে একদিন ইয়ানিক ও সাথীরা মহাকাশে এবেল ৩৭০ (Abell 370) গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের প্রান্তে অদ্ভুত আকৃতির এক বস্তুর সন্ধান পেলেন। বস্তুটি আকৃতিতে অস্বাভাবিক রকমের লম্বাটে এবং দেখতে বেশ খানিকটা বিকৃত – দেখতে অনেকটা লম্বাটে হাসির “স্মাইলির” মতো। বস্তুটি নিয়ে ভীষণরকম সমস্যায় পড়লেন এই তরুণ গবেষক দল, কারণ তাদের সঙ্গে থাকা জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত কোনো ক্যাটালগে এরকম কোনো বস্তুর উল্লেখ নেই। প্রথমে তারা ভেবেছিলেন যে হয়তো টেলিস্কোপের লেন্সের কোনো সমস্যার কারণে এমন ঘটছে। কিন্তু দ্রুতই তারা বুঝতে পারলেন যে সমস্যাটি লেন্স সংক্রান্ত নয়, বরং অন্যকিছু।
আলবার্ট আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (General Theory of Relativity) অনুসারে, স্পেস-টাইমের ভেতর যখন ভর বিশিষ্ট কোন বস্তু থাকে, তখন সেটি তার আশেপাশের স্পেস-টাইমকে (Space-time) বাঁকিয়ে ফেলে। ফলে যদি বিশাল ভরের কোন বস্তু কোন স্থানে থাকে তবে সেটা বিপুল শক্তিশালী মহাকর্ষ বল তৈরি করতে পারে। এর ফলে ওই স্থানটি এতবেশি বেঁকে যেতে পারে যে, তার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় আলোক রশ্মির গতিপথও অনেকটা বেঁকে যায়। ভারী কাঁচের (Lens) ভিতর দিয়ে ভ্রমণের সময় আলোক রশ্মির গতিপথ যেমন বেঁকে যায়, বিষয়টি অনেকটা সেইরকম। এটি মহাকর্ষীয় লেন্সিং (Gravitational Lensing) নামে পরিচিত।

ইয়ানিক ও তার সাথীরা ধারণা করলেন যে, এবেল ৩৭০ গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের প্রান্তে অদ্ভুত লম্বাটে আকৃতির বস্তুটি আসলে ক্লাস্টারটির আড়ালে লুকিয়ে থাকা কোনো গ্যালাক্সি। যেহেতু, এবেল ৩৭০ ক্লাস্টারটি ইয়ানিকদের মানমন্দির ও গ্যালাক্সিটির মধ্যবর্তী পথে একই সরলরেখায় অবস্থান করছে, এবেল ৩৭০ এর অতি শক্তিশালী মহাকর্ষ বল গ্যালাক্সিটি থেকে আসা আলোক রশ্মিটিকে এমন ভাবে বাঁকিয়ে ফেলছে যে টেলিস্কোপে গ্যালাক্সিটির এরকম একটি বিকৃত চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু, সমস্যাটা জটিল হয়ে দাঁড়ালো যখন তারা এবেল ৩৭০ ক্লাস্টারটি দ্বারা সৃষ্ট মহাকর্ষ বলের একটি হিসেব বের করলেন। তারা দেখলেন, একটি গ্যালাক্সি থেকে আসা আলোকে এভাবে বাঁকাতে হলে যে পরিমাণ মহাকর্ষ বলের প্রয়োজন এবং সেজন্য ক্লাস্টারে যে পরিমাণ “বস্তু বা পদার্থ” প্রয়োজন, এবেল ক্লাস্টারটির সর্বমোট পদার্থের পরিমাণ তার তুলনায় কয়েকগুণ কম। নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ইয়ানিক ও তার সাথীরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই ক্লাস্টারটিতে বিপুল পরিমাণ অদৃশ্য বস্তু বা ডার্ক ম্যাটার লুকিয়ে আছে, যার ফলে এই ক্ষেত্রে এরকম প্রচন্ড শক্তিশালী একটি মহাকর্ষ বলের সৃষ্টি হয়েছে।
৩
আইনস্টাইনের তত্ত্ব এবং মিনকোয়স্কি স্পেস-টাইম কন্টিনিউয়াম
দৈনন্দিন কাজে কোন কিছুর অবস্থান বুঝানোর জন্য আমরা সাধারনত দুই বা তিনটি স্থানাংক (মাত্রা) ব্যবহার করে থাকি। যেমন ধরা যাক, একটি পার্কে কোন একটি গাছের অবস্থান সম্পর্কে আমরা কাউকে একটি ধারণা দিতে চাই। সেক্ষেত্রে, হয়ত স্বাভাবিক ভাবে বলব, সোজা “এত” মিটার এগিয়ে গিয়ে ডানে বা বাঁয়ে “অত” মিটার এগিয়ে যান। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে আমরা দুইটি স্থানাংক বা মাত্রা ব্যবহার করছি। এখন যদি ঐ গাছেরই একটি ফলের অবস্থান আমাদের বলতে হয়, তাহলে দুই মাত্রা আর যথেষ্ট নয়, আমাদের নতুন আরেকটি মাত্রা যোগ (এক্ষেত্রে উচ্চতা) করে চলতে হয়ে “অত” মিটার উচ্চতায় ফলটি পাওয়া যাবে। কিন্তু, এই পদ্ধতির মাধ্যমে স্থির বস্তুর অবস্থান নির্ণয় সম্ভব হলেও, গতিশীল কোন বস্তুর অবস্থান নির্ণয় সম্ভব নয়। কারণ, আমরা যতক্ষনে তার অবস্থান সম্পর্কে কাউকে জানাবো ততক্ষনে বস্তুটি অন্য অবস্থানে চলে যাবে।
মনে করি, আমরা আকাশে চলমান একটি উড়োজাহাজের অবস্থান সম্পর্কে কাউকে তথ্য দিতে চাই। সেক্ষেত্রে উড়োজাহাজের অবস্থান জানাতে “অত ডিগ্রি দ্রাঘিমা”, “অত ডিগ্রি অক্ষাংশে” এবং “অত মিটার উচ্চতা” – এই তিনটি তথ্যের সাথে এটাও বলতে হবে ঠিক কয়টার সময় উড়োজাহাজটি ওই নির্দিষ্ট অবস্থানে ছিলো। তাই, গতিশীল বস্তুর অবস্থান বর্ননার জন্য অন্য তিনটি স্থানাংকের সাথে সাথে সময়ও একটি অপরিহার্য স্থানাংক। ১৯০৫ সালে আলবার্ট আইনস্টাইন তার বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের (Special Theory of Relativity) মাধ্যমে এই বিষয়টিকে সমন্বয় করে স্থান ও সময় সম্পর্কে এক যুগান্তকারী নতুন ধারণা দেন। তিনি বলেন যে, সময় কোনো বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নয়, স্থান থেকে সময়কে আলাদা করা যায় না। স্থান ও সময় মিলে একত্রে একটি ভিন্ন ধরনের সমন্বিত বস্তু (Object) বা স্পেস-টাইম (Space-Time) কাঠামো তৈরি করে। ১৯০৭ সালে জার্মান গণিতবিদ হারম্যান মিনকোয়স্কি (আইনস্টাইনের ভূতপূর্ব শিক্ষক) তিন মাত্রার ইউক্লিডিয়ান স্পেস এর সাথে সময়কে (টাইম) যোগ করে চার-মাত্রার স্পেস-টাইম ফ্রেমওয়ার্ক (Space-time framework) প্রস্তাব করেন যা বর্তমানে মিনকোয়স্কি স্পেস-টাইম কন্টিনিউয়াম (Space-time continuum) হিসেবে পরিচিত।
আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব দারুণভাবে সফলতা পেলেও, আইনস্টাইন জানতেন যে তার এই তত্ত্বে একটি অসামঞ্জস্য রয়েছে। এই তত্ত্বের সাথে মহাকর্ষ বলের পরিপূর্ণ সমন্বয় হচ্ছিলো না। নিউটিনের মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে, দুটি বস্তুর পরস্পরের উপর আকর্ষণ বল তাদের দূরত্বের সমানুপাতিক। ফলে, পরস্পরকে আকর্ষণ করছে এমন দুটি বস্তুর কোন একটিকে যদি তার নিজস্ব অবস্থান থেকে সরানো হয় তাহলে তার প্রভাব “সাথে সাথে” (Instantaneously) অন্য বস্তুটির উপর পড়বে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে, আলোর গতিই সর্বোচ্চ গতিসীমা, কোন কিছুই এই সীমাকে অতিক্রম করতে পারেনা। আলো যত দ্রুত গতিতেই ভ্রমণ করুক না কেন, এই “সাথে সাথে” ব্যাপারটি তার চেয়েও দ্রুত, কেননা এই ঘটনাটি ঘটার জন্যে কোন সময়েরই প্রয়োজন হচ্ছে না। কারণ, আলোর গতি যতই দ্রুত হোক না কেন, তা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গার যেতে “অতি সামান্য” হলেও কিছু না কিছু সময় নিবে। এই সমস্যার সমাধানের জন্যে ১৯১৫ সালে আইনস্টাইন তার আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের সাথে মহাকর্ষ বলের সমন্বয় ঘটিয়ে সফল ভাবে যুগান্তকারী এক তত্ত্ব দিতে সক্ষম হন যা পরবর্তীতে সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (General Theory of Relativity) নামে পরিচিতি লাভ করে।
নতুন তত্ত্বে আইনস্টাইন মহাকর্ষ বলের এক বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন যে, মহাকর্ষ শক্তি অন্যান্য শক্তি বা বল থেকে ভিন্ন ভাবে ক্রিয়া করে। তার মতে, আমরা সাধারণ চিন্তায় যেরকম ভাবি যে, স্পেস-টাইম ফ্লাট বা সমতল ধরনের কিছু, বাস্তবে কিন্তু এর গঠন সেরকম নয়। এই তত্ত্বের সবচেয়ে চমকপ্রদ কিছু বিষয় হলো –
নিউটনের সূত্র অনুসারে আমরা জানি, গ্রাভিটি বা মহাকর্ষ বলের কারণে সৌরজগতে গ্রহগুলো সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসে। কিন্তু, স্পেস-টাইম ফ্রেমওয়ার্কে বিষয়টি একটু অন্যভাবে কাজ করে। বাস্তব ক্ষেত্রে সূর্য তার নিজস্ব ভর ও শক্তির কারণে তার চারিপাশের স্পেসকে বাঁকিয়ে ফেলে। সেই বাঁকানো স্পেসে পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহগুলো সরলরেখা বরাবরই চলতে থাকে। কিন্তু, যেহেতু সূর্যের চারিপাশে স্পেস নিজেই বাঁকা, পৃথিবী বা গ্রহগুলো সোজা পথে চললেও ওই বাঁকা স্পেসের কারণে সূর্যের চারিপাশে ঘুরে আশে।
একইভাবে বড় কোন মহাজাগতিক বস্তুর পাশ দিয়ে চলার সময় আলোক রশ্মিও বাঁকা স্পেস-টাইমের মধ্যে সরল রেখায় না চলে, খানিকটা বেঁকে যায়। সেই কারণে দূরের কোন নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আসা আলোক রশ্মি সূর্যের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময়েও খানিকটা বেঁকে যাবে। যদি তাই হয়, সূর্যের আশেপাশে আমরা যেসব নক্ষত্রকে দেখতে পাই, আপাতদৃষ্টিতে আমরা সেই নক্ষত্রকে যে অবস্থানে দেখি, তার আসল অবস্থান সেখান থেকে কিছুটা ভিন্ন হবে।

এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ১৯৩০ এর দশকে আইনস্টাইন অনুমান করেন যে, দুইটি মহাজাগতিক বস্তুর মধ্যবর্তী স্থানে বিশাল ভরের অন্য কোন মহাজাগতিক বস্তু (যেমনঃ গ্যালাক্সি বা গ্যালাক্সি ক্লাস্টার) অবস্থান করলে তা বস্তু দুইটির মাঝে অনেকটা লেন্সের মতো কাজ করবে এবং একটি বস্তু থেকে অন্য বস্তুকে দেখার সময় তা অন্য বস্তুটির প্রতিকৃতিকে অনেকখানি বিকৃত করে ফেলবে। ফলে অন্যপাশের বস্তুটিকে লম্বাটে, বাঁকানো এমনকি একাধিক বস্তু বলে মনে হতে পারে। ১৯৭৯ সালে বিজ্ঞানীরা মহাকাশে প্রথম এ ধরনের একটি মহাকর্ষ লেন্স আবিস্কার করেন। তারা দেখতে পান যে আকাশে খুব কাছাকাছি অবস্থানে এমন দুটি কোয়েসার রয়েছে যাদের দূরত্ব ও বর্ণালী একইরকম। ভালভাবে পরীক্ষা করে তারা নিশ্চিত হন যে, আসলে এই দুইটি চিত্র একই কোয়েসারের, মধ্যবর্তী কোনো স্থানে মহাকর্ষীয় লেন্সিং এর কারণে তাদের দুটি কোয়েসার বলে মনে হচ্ছে। পরবর্তীকালে মহাকাশে এই ধরনের মহাকর্ষীয় লেন্সের সাহায্যেই বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বে ডার্ক ম্যাটারের অবস্থান নির্ণয় করে এর বন্টন বা বিন্যাসের বেশ কিছু মানচিত্র তৈরি করেছেন। এবেল ১৬৮৯ গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের ভিতরে ডার্ক ম্যাটারের বিন্যাসের এমন একটি এখানে দেখানো হলো।

মহাকর্ষীয় লেন্স ব্যবহার করে ২০০২ সালের জুন মাসে নাসার বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকে ২.২ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এবেল ১৬৮৯ গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের ভিতরে ডার্ক ম্যাটারের বিন্যাসের একটি চিত্র প্রকাশ করেন। বিশাল এই গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের ভিতরে প্রায় এক হাজার গ্যালাক্সি রয়েছে। ক্লাস্টারের পেছনে থাকা ৪২টি গ্যালাক্সির লেন্সের কারণে সৃষ্ট নানা ধরনের ১৩৫টি ছবি পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানীরা এই চিত্রটি তৈরি করেন। এখানে দেখা যায় যে, ক্লাস্টারটির কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ডার্ক ম্যাটারের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি।
৪
ডার্ক এনার্জি
রহস্যময় এই এনার্জি সম্পর্কে আমরা খুব সামান্যই জানি। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের হার বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র জানতে পেরেছেন যে, আমাদের এই মহাবিশ্বে মোট পরিমাণ কি ডার্ক এনার্জির রয়েছে। ব্যাস এতটুকুই! বাকীটা পুরোপুরি রহস্য।
২০০৩ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যখন উইলকিনসন মাইক্রোওয়েভ অ্যানিসোট্রপি প্রোব বা WMAP থেকে প্রাপ্ত সব তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষন করে তার ফলাফল হাতে পেলেন, তারা বিস্ময়ে রীতিমত হতবাক হয়ে গেলেন। কারণ, কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনের যে ম্যাপটি তারা হাতে পেলেন সেখান থেকেই বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মত প্রায় নির্ভুল ভাবে মহাবিশ্বের বয়স নির্ণয় করতে সক্ষম হন এবং আমরা জানতে পারি যে মহাবিশ্বের বয়স এখন ১৩.৭ বিলিয়ন বছর।
একদিকে WMAP যেমন দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা নানা বিতর্কের সমাধান করলো, একই সাথে এটি জ্যোতির্বিদ্যার জগতে আরও একটি বিরাট বিস্ময় ও রহস্যের জন্ম দিলো। বিজ্ঞানীরা প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন যখন তারা জানতে পারলেন যে, আমাদের জানা ও ধারণার মধ্যে থাকা মহাবিশ্বের যত ধরণের পদার্থ ও শক্তি আছে, তার বাইরেও সম্পূর্ণ অচেনা, অনাবিষ্কৃত ও ধরা ছোঁয়ার বাইরে আরও এক ধরণের পদার্থ ও শক্তি রয়েছে, যা আমাদের এই মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ও গঠনের মূল ভিত্তি!
WMAP এর তথ্য থেকেই বিজ্ঞানীরা প্রথম নিশ্চিত হন মহাবিশ্বের এই অজানা ৯৫% উপদান সম্পর্কে। আমরা আগের পর্বে দেখেছি যে, এই অজানা উপাদানের মধ্যে ২৫% ডার্ক ম্যাটার। বিজ্ঞানীরা এখন জানতে পারলেন এই সাথে রয়েছে আরও একটি অজানা উপাদান, যাকে তারা বললেন ডার্ক এনার্জি – যা মহাবিশ্বের প্রায় ৭০% অংশ। WMAP থেকে পাওয়া এই সব অদ্ভুত তথ্য সম্পর্কে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী জন বাহকাল বলেন, “আমরা একটি অকল্পনীয়, উন্মাদ মহাবিশ্বে বাস করি, কিন্তু যার নিরূপক বৈশিষ্টগুলো এখন আমরা বুঝতে শুরু করেছি।“ তবে, WMAP থেকে পাওয়া তথ্যগুলোর মধ্যে যে তথ্যটি বিজ্ঞানীদের একেবারে কাঁপিয়ে দিয়েছিলো অথবা বলা যায় এলোমেলো করে দিয়েছিল তা হলো ওই ৭০% ডার্ক এনার্জি, যা কিনা এককভাবেই মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ ও শক্তির চার ভাগের প্রায় তিন ভাগ! এই ডার্ক এনার্জি হলো শুন্যস্থানের মধ্যে লুকিয়ে থাকা শক্তি এবং যাকে কোনভাবে দেখা যায়না বা পরীক্ষাগারে সনাক্ত করা যায়না। বিজ্ঞানীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মনে করেন যে, ডার্ক এনার্জির আসলে “স্থানের (Space)“ একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।
আইনস্টাইনের কসমোলজিক্যাল ধ্রুবক
আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রথম দিকে আইনস্টাইন মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব (Cosmology) নিয়ে গভীরভাবে কাজ করছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি তার আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের (General Theory of Relativity) স্পেস-টাইম ধারণা ব্যবহার করে ১৯১৭ সালে মহাবিশ্বের আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে একটি কাঠামো প্রস্তাব করেন। আইনস্টাইন যখন তার এই কাঠামোটি প্রস্তাব করেন, তখন কেউই ধারণা করেন নাই যে, মহাবিশ্ব আসলে সম্প্রসারণশীল বা আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি নিজেও তার গভীর ধর্মবিশ্বাসের কারণে মনে করতেন যে, মহাবিশ্ব শাশ্বত, স্থির ও অপরিবর্তনীয়। ফলে স্বাভাবিক কারণেই আইনস্টাইন এমন একটি কাঠামো প্রস্তাব করেন যা তার ধারণা ও বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।
কিন্তু, আইনস্টাইনের জানতেন যে, তার প্রস্তাবিত কাঠামোয় একটা বড় সমস্যা ছিল। কারণ, এই কাঠামোতে মহাকর্ষ বল সবসময় আকর্ষণমূলক। ফলে, যে সমস্যাটি সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল তা হলো, যদি মহাকর্ষ বল শুধু আকর্ষণমূলকই হয়, তাহলে কোন রকম সাহায্য ছাড়াই মহাকাশে বিলিয়ন বিলিয়ন নক্ষত্র ও অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তু টিকে আছে কিভাবে? তাদের তো সব একসাথে ধ্বসে পড়ার কথা! এই সমস্যা থেকে উত্তরনের জন্য আইনস্টাইন এক নতুন ধরনের বিকর্ষণমূলক বলের ধারণা করলেন, যা মহাকর্ষ বলের এই আকর্ষণমূলক শক্তিকে প্রতিরোধ করে একটি স্থির ও অপরিবর্তনীয় কাঠামোর মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে পারে। এই বিকর্ষণমূলক বলের জন্য তিনি একটি নতুন টার্মের প্রস্তাব করলেন, যাকে তিনি নাম দিলেন “কসমোলজিক্যাল টার্ম (Cosmological Term)” এবং তার সমীকরণে একটি ধ্রুবক যোগ করলেন যাকে তিনি বললেন “কসমোলজিক্যাল ধ্রুবক (Cosmological Constant)” । যদিও এই ধ্রুবকটি সমীকরণে কৃত্রিমভাবে যোগ করা হয়েছিল, তবুও অন্য কোন গ্রহনযোগ্য সমাধান না থাকায় সাময়িকভাবে বিজ্ঞানী মহলের অনেকেই এটা মেনে নিয়েছিলেন। এদিকে ১৯২০ সাল নাগাদ আইনস্টাইনের মনোযোগও মহাবিশ্ব থেকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সে সরে যায়, ফলে এই বিষয়টি নিয়ে তিনি নিজেও আর মাথা ঘামান নি।
অনেকেই আইনস্টাইনের “কসমোলজিক্যাল টার্ম” মেনে নিলেও, সবাই যে মেনে নিয়েছিলেন এমন কিন্তু নয়। বিশেষত, ইউরোপের কিছু পদার্থ বিজ্ঞানী প্রথম থেকেই এর বিরোধিতা করে আসছিলেন, যাদের একজন হলেন বেলজিয়ান গণিতবিদ মনসিনর জর্জ লেমাইত্রে (Monsignor Georges Lemaitre)। মহাবিশ্বের কাঠামো ব্যাখ্যায় লেমাইত্রে আইনস্টাইনেরই সমীকরণ ব্যবহার করেন, তবে তিনি তার চিন্তা শুধুমাত্র স্থির ও অপরিবর্তনীয় মহাবিশ্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। ফলে, ১৯২৭ সাল নাগাদ তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, আইনস্টাইনের “কসমোলজিক্যাল টার্ম” মোটেই কোন স্থিতিশীল ধ্রুবক নয়। সামান্য একটু এদিক ওদিক হলেই হয় মহাবিশ্ব ধ্বসে পড়ে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে, নাহয় সমস্ত কাঠামো ভেঙ্গে অনন্ত কাল ধরে বিশৃঙ্খল ভাবে ছুটে বেড়াবে।
এইসব বিতর্কের মধ্যেই আইনস্টাইন হাবলের আবিষ্কার সম্পর্কে জানতে পারেন এবং সরেজমিনে তার গবেষণার ফলাফল দেখেন। খুব সহজেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, স্থির ও অপরিবর্তনীয় মহাবিশ্বের মতবাদে অনমনীয় না থেকে যদি তিনি তার নিজেরই তত্ত্ব ও সমীকরণের উপরই পূর্ন আস্থা রাখতেন, তাহলে কসমোলজিক্যাল টার্মের কোন প্রয়োজনই পড়তো না এবং তিনি নিজে সহজেই মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের বিষয়টি বুঝতে পারতেন। ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই আবিস্কারটিও তার হাতের মুঠোর মধ্যেই ছিল, কিন্তু নিজের ভুলেই তা তার হাতের মুঠোগলে বেরিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে আইনস্টাইন এই কসমোলজিক্যাল টার্মকে তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল (Greatest Blunder) বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।
যদিও আইনস্টাইন তার কসমোলজিক্যালকে টার্মকে পরিত্যাগ করলেন, কিন্তু তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন যে, “শূন্য স্থান (Empty Space)“ আসলে শূন্য নয়, বরং এটি “কিছু একটা” যার বেশ কিছু চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তিনি বুঝতে পারেন যে, শূন্য স্থানের ভিতরে নতুন করে আরও “স্থান (Space)“ তৈরি হতে পারে এবং শূন্য স্থানের এক ধরনের “নিজস্ব শক্তি” রয়েছে। যেহেতু, এই শক্তি শূন্য স্থানের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, স্থানের সম্প্রসারণের সাথে সাথে এই শক্তির ঘনত্ব কমবে না, বরং সমহাবিশ্বে স্থান যত সম্প্রসারিত হতে থাকবে, একই সাথে স্থানের নিজস্ব এই শক্তিও তৈরি হতে থাকবে। ফলে, যত বেশি শক্তি তৈরি হবে, স্পেস বা স্থানকে তা তত বেশি দ্রুত হারে সম্প্রসারণ করতে থাকবে।
রহস্যময় এন্টি গ্রাভেটি ও ডার্ক এনার্জি
WMAP থেকে প্রাপ্ত তথ্য যে আমাদের মহাবিশ্বের উৎপত্তিকালের প্রায় নির্ভুল একটি ধারণা দিয়েছিল শুধু তাই নয়, সেই সাথে আমরা এটাও জানতে পারলাম মহাবিশ্বের পরিসমাপ্তিটাও কি ধরনের হতে পারে। এক রহস্যময় বিকর্ষণমূলক মহাকর্ষ বল (Antigravity) বিং ব্যাগ এর পর নতুন সৃষ্টি হওয়া শিশু মহাবিশ্বে গ্যালাক্সিগুলোকে অকল্পনীয় দ্রুত গতিতে দূরে ঠেলে দিচ্ছিল। কিছুদিন আগেও জ্যোতির্বিদরা মনে করতেন যে, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের এই হার ধীরে ধীরে কমে আসছে। কিন্তু, WMAP থেকে প্রাপ্ত তথ্য আমাদের জানালো, বিগ ব্যাং এর পর একসময় মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ শ্লথ বা ধীর হয়ে আসতে থাকলেও, ৬.৫ বিলিয়ন বছর আগে, কোন এক রহস্যময় বিকর্ষণমূলক মহাকর্ষ বলের (Antigravity) প্রভাবে মহাবিশ্ব প্রসারণের হার নতুন করে বাড়তে থাকে। এই প্রসারণ ডি-সিটার প্রসারণ (de Sitter Expansion) নামে পরিচিত। বিজ্ঞানীদের ধারণা, সম্প্রসারণের গতি হঠাৎ এভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণ কোনো এক ধরনের রহস্যময় ডার্ক ফোর্স। বিজ্ঞানীদের ধারণা করা এই ডার্ক ফোর্সের মান ও ধরণ আশ্চর্যজনক ভাবে আইনস্টাইনের কসমোলজিক্যাল ধ্রুবকের সমান।

শূন্য স্থানের ভেতরে কিভাবে শক্তি তৈরি হয়, সে বিষয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্ব (Quantum Theory) ব্যবহার করে অন্য আরেকটি তত্ত্ব দেয়া হয়েছিলো, যেখানে বলা হয়েছিলো শূন্য স্থানে অবিরামভাবে নানা ধরনের অস্থায়ী “ভার্চুয়াল (Virtual)” কণিকা তৈরি হয় ও ধ্বংস বা বিলিন হয়ে যায়। কিন্তু যখন পদার্থবিজ্ঞানীরা এ ধরনের শূন্য স্থানের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির একটি গাণিতিক হিসেব বের করলেন, তারা দেখতে পেলেন যে, হিসেবে বিশাল রকমের হেরফের রয়েছে। তারা যে সংখ্যাটি পেলেন সেটি আসলের চেয়ে প্রায় ১০১২০ গুণ বেশি, অর্থাৎ ১ সংখ্যাটির পর ১২০টি শূন্য যোগ করলে যা হয়, ততগুণ বেশি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এটি হলো পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসের দূর্বলতম ভবিষ্যদ্বাণী। তাই ধরে নেয়া যায়, এই তত্ত্বটি সঠিক নয়। ডার্ক এনার্জিকে ব্যাখ্যা করতে আরও কিছু নতুন তত্ত্ব দেয়া হয়েছে, কিন্তু সেগুলোর কোনটিই উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি।
ফলে, ডার্ক এনার্জির রহস্য ব্যাখায় এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে শক্তিশালী দাবিদার হলো আইনস্টাইনের কসমোলজিক্যাল ধ্রুবক (Cosmological Constant)। মজার ব্যাপার হলো যাকে আইনস্টাইন তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল আখ্যা দিয়ে বাতিল করে দিয়েছিলেন, সেটা কি অদ্ভুত ভাবেই না ফিরে আসলো আবার! হতে পারে তিনি যে উদ্দেশ্যে এই টার্মটি ব্যবহার করেছিলেন, সেখানে এটার প্রয়োজন ছিলো না; কিন্তু শক্তিটির অস্তিত্ব এখন পুরোপুরি অনস্বীকার্য। বিজ্ঞানীরা আরও মনে করেন যে, মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াবে, তার প্রধান নিয়ামক হবে এই ডার্ক এনার্জি। যদি তাই হয়, তবে কি অদূর ভবিষ্যতে আইনস্টাইনের জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলই তার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন (Greatest Trump) বলে বিবেচিত হবে?
সময়ই বলে দিবে এ প্রশ্নের উত্তর।
—
দেশের বই পোর্টালে লেখা পাঠাবার ঠিকানা : desherboi@gmail.com
কপিরাইট © ২০১৭ - ২০২০ ।। বইদেশ-এ প্রকাশিত কোনও সংবাদ, কলাম, তথ্য, ছবি, কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না
Design & Development by: TeamWork BD